থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘাত বাংলাদেশের জন্য বার্তা
ব্রি. জে. (অব.) রোকন উদ্দিন [প্রকাশ : দেশ রূপান্তর, ৩১ জুলাই ২০২৫]
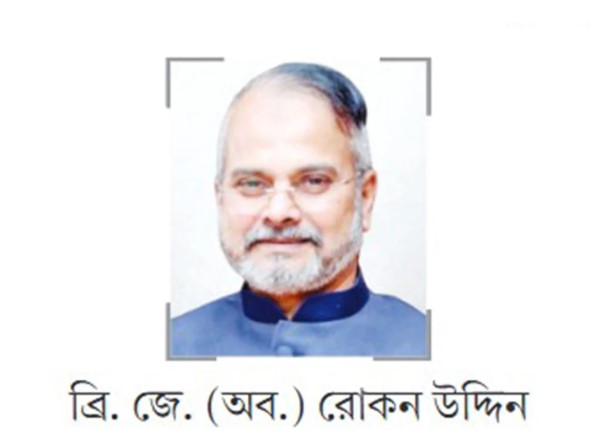
সম্প্রতি থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা এবং সাবেক কম্বোডিয়ান প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের মধ্যে ফাঁস হওয়া ফোনালাপ এবং পরে হুন সেনের উসকানিমূলক ফেসবুক লাইভ পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নাড়া দিয়েছে। যাদের মধ্যে একসময় ছিল ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, আজ সেই সম্পর্কই ভেঙে পড়েছে। এই ভাঙন শুধু ব্যক্তিগত বিরোধ নয়—এটি একটি কাঠামোগত ব্যর্থতা, যা পুরো অঞ্চলের কৌশলগত ভারসাম্যকে দুর্বল করছে।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া দ্বন্দ্বের মূল শিকড় ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও জাতীয় আত্মপরিচয়ের সংঘাতে নিহিত। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে ‘প্রে-ভিহিয়ার’ মন্দির—ড্যাংরেক পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় স্থান। ১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ) এই স্থান কম্বোডিয়ার আওতায় ঘোষণা করলেও থাইল্যান্ডে এ সিদ্ধান্ত এখনো প্রশ্নবিদ্ধ। ফরাসি ঔপনিবেশিক মানচিত্রের ভিত্তিতে দেওয়া এই রায়কে থাইল্যান্ড ‘ইতিহাস বিকৃতি’ হিসেবে মনে করে। ২০০৮-১১ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার সীমান্তে সংঘর্ষ হয়েছে, প্রাণহানিও ঘটেছে। আজও সেই বিরোধ রয়ে গেছে এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
কূটনৈতিক বিরোধ থেকে ভূরাজনৈতিক সংঘাতে রূপান্তর
এই দ্বন্দ্ব আজ আর শুধু মন্দির বা সীমান্ত নিয়ে বিরোধ নয়—এটি একটি কৌশলগত যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন সরাসরি প্রভাব ফেলছে। যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যান্ডকে ‘ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল’-এর অংশ হিসেবে দেখে, যেখানে কম্বোডিয়া চীনের একটি বিশ্বস্ত মিত্র, বিশেষ করে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (BRI) আওতায়। এই দ্বন্দ্ব এখন অনেক বিশ্লেষকের চোখে ‘প্রক্সি যুদ্ধ’-এর আকার ধারণ করছে। কিন্তু এর ফলে স্থানীয় প্রেক্ষাপট ভুলভাবে সরলীকৃত হচ্ছে এবং ছোট দেশগুলোকে শুধু ‘মাঠের খেলোয়াড়’ বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু বিদেশি হস্তক্ষেপকেই বৈধতা দেয় না, বরং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও নষ্ট করে।
আঞ্চলিক প্রভাব ও বাংলাদেশের জন্য বার্তা
যদিও বাংলাদেশ এই সংঘাত থেকে ভৌগোলিকভাবে দূরে, তবে এর কৌশলগত প্রভাব আমাদের ওপরও পড়তে বাধ্য।
১. ভূরাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া : থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘাত সরাসরি যুদ্ধে রূপ নিলে কিংবা বড় শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বাড়লে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন সংঘাতে প্রক্সিযুদ্ধের রূপ নিতে পারে, যার ফলে আঞ্চলিক শান্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ ও সাগরপথ নিরাপত্তাহীন হয়ে উঠতে পারে। এর সরাসরি প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়বে—বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে আমাদের নৌবাণিজ্য ও কৌশলগত অবস্থান ঝুঁকির মুখে পড়বে।
২. আসিয়ানের অকার্যকারিতা : বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কৌশলগতভাবে যুক্ত হতে চায় এবং ভবিষ্যতে আসিয়ানে সদস্যপদ লাভ করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংকট যেভাবে আসিয়ানকে নিষ্ক্রিয় ও প্রভাবহীন করে ফেলেছে, তা আমাদের সতর্ক করে দেয়। শুধু কাগজে চমৎকার নীতিমালা থাকলেই চলবে না—জরুরি সংকটে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার সক্ষমতা থাকতে হবে। আসিয়ানের ব্যর্থতা দেখিয়ে দেয়, কোনো আঞ্চলিক সংগঠনের কার্যকারিতা নির্ভর করে তার সদস্যদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর।
৩. প্রক্সি জালে না জড়িয়ে কৌশলগত স্বাধীনতা : আজকের ভূরাজনীতিতে সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে ছোট ও মাঝারি শক্তিগুলোর প্রক্সিযুদ্ধের মোহে জড়িয়ে পড়া। বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, রাশিয়া কিংবা অন্য শক্তির একপক্ষীয় আশ্রয়ে না গিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ, স্বাধীন এবং সার্বভৌমভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে। নিজস্ব স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে একটি ‘বাংলাদেশকেন্দ্রিক কৌশলগত দর্শন’ তৈরি করতে হবে। প্রক্সি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া মানেই আত্মনির্ভরতার বিসর্জন দেওয়া—এটা আমাদের কৌশলগত নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি।
৪. বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তা : বঙ্গোপসাগর এখন একটি নতুন ভূকৌশলিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যেখানে ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এমনকি রাশিয়ারও সরাসরি স্বার্থ জড়িত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৌবাহিনীগুলোর আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা (যেমন : কম্বোডিয়ার চীনা সমর্থিত রিয়াম নৌঘাঁটি, থাইল্যান্ডের ইউএস জাহাজের প্রবেশাধিকার) সরাসরি বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশের বন্দর, সামুদ্রিক সম্পদ ও নৌচলাচল পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে এখনই বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক প্রতিরক্ষা নীতি, নৌ-আধুনিকায়ন এবং কৌশলগত অংশীদারত্ব গড়ে তোলা জরুরি।
৫. মানবিক সংকটের সম্ভাবনা : কম্বোডিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংঘাত অতীতে উদ্বাস্তু প্রবাহ তৈরি করেছিল। যদি এখন আবার সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে, তবে তা শুধু ভৌগোলিকভাবে কম্বোডিয়া-ভিয়েতনাম-লাওস অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না—বরং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক মন্দা, মানব পাচার, অস্ত্র পাচার, এমনকি সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলবে। এ ধরনের মানবিক সংকট দক্ষিণ এশিয়া হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আমাদের সীমান্তে শরণার্থী সংকট (যেমন রোহিঙ্গা) ইতোমধ্যেই জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি তৈরি করেছে; নতুন সংকট প্রতিরোধে আমাদের কূটনৈতিক প্রস্তুতি ও মানবিক প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাও শক্তিশালী করতে হবে।
বৈশ্বিক শক্তির ভূমিকা
যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি কৌশলগত পদক্ষেপকে নিজেদের প্রভাব বলয়ে দেখতে চায়। চীন কম্বোডিয়াকে ব্যবহার করে ইন্দো-প্যাসিফিকে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চায়, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যান্ডের মাধ্যমে এই কৌশল রুখতে চায়। রাশিয়া, ভারতসহ আরো কিছু শক্তি এখন সুনিপুণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় প্রতিটি দেশকে শুধু একক শক্তির ওপর নির্ভর না করে বহুমেরুকেন্দ্রিক কূটনীতিকে সামনে আনতে হবে। এই বহুমেরুকেন্দ্রিকতা মানে এক শক্তির জায়গায় আরেক শক্তি নয়—বরং নিজস্ব সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা।
শান্তির সম্ভাবনা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা
থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব, যদি উভয় দেশ অহংকারের দেয়াল ভেঙে বাস্তবতা ও জনগণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। যুদ্ধ বা উত্তেজনা নয়—সমঝোতা ও সংলাপই হতে পারে টেকসই সমাধানের পথ। সীমান্ত-সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনে একটি যৌথ সীমান্ত কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যেখানে আসিয়ানের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক দল যুক্ত থাকবে। এতে সীমানা চিহ্নিতকরণ ও অবকাঠামোগত সমস্যা নিরসনের পাশাপাশি পারস্পরিক আস্থাও গড়ে উঠবে। আরেকটি সম্ভাব্য উদ্যোগ হতে পারে—বিতর্কিত ঐতিহাসিক স্থানগুলোর যৌথ ব্যবস্থাপনা। উদাহরণস্বরূপ, প্রেহ ভিহার মন্দির এলাকাকে ‘শান্তি অঞ্চল’ হিসেবে ঘোষণা করে উভয় দেশ সেখানে পর্যটন, গবেষণা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হতে পারে। এতে জাতীয় গর্ব যেমন অক্ষুণ্ণ থাকবে, তেমনি সংঘাতের সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে।
তবে এসব প্রচেষ্টায় বাইরের শক্তি যেমন যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের মধ্যস্থতার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বিপজ্জনক হতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ প্রায়ই নিজের স্বার্থ রক্ষায় পরিচালিত হয়, যার ফলে প্রকৃত সমাধান পিছিয়ে পড়ে। সুতরাং, আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে আঞ্চলিক নেতৃত্ব ও উদ্যোগই হওয়া উচিত মূল ভিত্তি। আসিয়ানের ভূমিকা পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে তারা শুধু বিবৃতি নয়, বাস্তব কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়। সর্বোপরি, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ইতিহাসের ভারসাম্যপূর্ণ মূল্যায়ন এবং আঞ্চলিক সংহতির প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকার।
বাংলাদেশের করণীয়
বাংলাদেশের জন্য এই সংঘাত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। শুধু বাহ্যিক শক্তির ভরসায় নয়, বরং নিজের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ও কূটনৈতিক ভারসাম্যকে শক্তিশালী করতে হবে। সাইবার ও সামরিক নিরাপত্তা, কৌশলগত কূটনীতি এবং স্বনির্ভরতা—এগুলোই আগামী দিনের আত্মরক্ষার মূল হাতিয়ার। বাংলাদেশের জন্য থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘাত একটি সতর্কবার্তা। বিশ্ব রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে শুধু বাহ্যিক বন্ধুত্বের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের প্রয়োজন স্বনির্ভর প্রতিরক্ষা নীতি, আধুনিক সাইবার ও সামরিক সক্ষমতা এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক। একদেশীয় নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের উচিত বহুমাত্রিক অংশীদারত্ব গড়ে তোলা, যাতে কোনো বৈশ্বিক উত্তেজনা আমাদের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত না করে।
থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া দ্বন্দ্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—আধিপত্যের যুগে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ধরে রাখা। বাংলাদেশকে এখনই ভাবতে হবে—আমরা কি একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভর রাষ্ট্র হব, নাকি আরেকটি মোহাচ্ছন্ন ‘জিও-পলিটিক্যাল বোর্ড’-এর ঘুঁটি? আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একটিমাত্র প্রশ্নের ওপর : আমরা কি নিজেদের পরিচয় ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারব?
লেখক : নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও গবেষক