সংবিধান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কেন
বর্তমান সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকার এবং তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারগুলো সংশোধন করে ‘মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা’ নামে একটি একক অধিকারের সনদ গঠন করা, যা আদালতে বলবৎযোগ্য হবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার ও নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে বিদ্যমান তারতম্য দূর হয়। বিষয়টি এখনো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনায় আসেনি। আশা করা যায়, রাজনীতিকরা তাদের প্রজ্ঞা দিয়ে জাতির কল্যাণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব [প্রকাশ : নয়াদিগন্ত, ১৮ জুলাই ২০২৫]
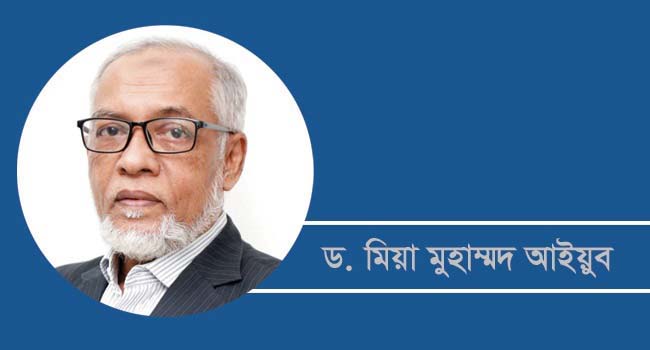
(শেষ কিস্তি)
প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তিতে সংবিধান সংস্কার প্রসঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, সংসদে নারী আসন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ তথা সংসদে নিজ দলের বিপক্ষে ভোটদান, সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতির পদ বিরোধী দলকে দেয়া, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আসনগুলোর সীমানা নির্ধারণ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোনো ব্যক্তির দণ্ড মার্জনা, বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও জরুরি অবস্থা জারি সংক্রান্ত বিধান ইত্যাদি মোট ১৩টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আজ শেষ কিস্তিতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা, প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান, সংবিধান সংশোধন, প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করব।
চৌদ্দ : ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে মন্ত্রিসভা-শাসিত সরকার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এ ব্যবস্থায় সরকারপ্রধান থাকেন প্রধানমন্ত্রী। তবে মন্ত্রিসভা সামষ্টিকভাবে পার্লামেন্ট তথা জনগণের কাছে জবাবদিহি করে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের প্রধান থাকেন রাজা বা রানী। তিনি মূলত কোনো নির্বাহী ক্ষমতা উপভোগ করেন না। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে আলঙ্কারিক পদে থেকে দায়িত্ব পালন করেন। ব্রিটেনে বিরোধী দলকেও বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়। সেখানে বিরোধী দলকে বলা হয় ‘অপজিশন অব দ্য কিং’।
১৯৭২ সালে বাংলাদেশের যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় তাতে ব্রিটিশ ধাঁচের পার্লামেন্টারি পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়। পার্থক্য ছিল যে, ব্রিটেনে রাজা বা রানী রাষ্ট্রপ্রধান, আর বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান। প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানে একই পদ্ধতি রয়েছে। লক্ষ করার বিষয় হলো- ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে মাত্র দুটো ক্ষেত্রে ক্ষমতা দেয়া হয় : ১. জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং ২. দেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ। অপর সব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক দায়িত্ব পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূলক।
১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করেন। ১৯৭২ সালের সংবিধান নামে সংসদীয় কাঠামো প্রবর্তন করলেও কার্যত তা যে ছিল না; সে সম্পর্কে রাজনীতিক ও লেখক মওদূদ আহমদ বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারব্যবস্থায় যেমন রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ ঘটে, ঠিক তেমনি ঘটেছে এ ক্ষেত্রে- ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে।’
২০২৪ সালে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে, ‘প্রধানমন্ত্রীর হাতে এ কেন্দ্রীভ‚ত ক্ষমতা শুধু সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ নয়, পুরো সংবিধানজুড়ে ছিল এবং সেটি বাংলাদেশে পরবর্তীকালের অগণতান্ত্রিক শাসন ডেকে এনেছে, পুঞ্জীভ‚ত করেছে।’ সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে কিভাবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছিল তার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তা হলো- “সংবিধানে আরেকটি মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে ‘নির্বাচিত একনায়কের’ ক্ষমতা দিয়ে সর্বশক্তিমান করে ফেলার ব্যবস্থা করা। ১৯৭২ সালে যখন সংবিধানটি প্রণয়ন করা হয়, তখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে যখন সেটি বঙ্গবন্ধুর কাছে পেশ করেছিল, তখন যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে কেটেছেঁটে সেগুলোয় পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির তুলনায় একচ্ছত্র (অ্যাবসোলুট অ্যান্ড আনচ্যালেঞ্জড) করার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাহীন বানিয়ে ফেলা হয়েছিল।”
শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে দিলেও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল রাখেন। বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে সংবিধান সংশোধন করে আবার সংসদীয় পদ্ধতি ফিরিয়ে আনেন। তবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার যে বিধান করা হয়েছিল; তা বহাল করা হয়। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এমনভাবে চর্চা করেন; যাতে ‘নির্বাচিত একনায়ক’ হিসেবে পরিচিতি পান। এরপর ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি প্রহসনের নির্বাচন করে তিনি জাতির সাথে প্রতারণা করেন। চ‚ড়ান্তভাবে ফ্যাসিবাদের রূপ পরিগ্রহ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এতটাই ক্ষমতাধর ছিলেন যে, পৃথিবীর কোনো প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের এরূপ ক্ষমতার দৃষ্টান্ত ছিল বিরল।
এসব বিষয় বিবেচনা করে সংবিধান সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধি বাড়ানোর সুপারিশ করেছে। ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ভারসাম্যমূলক ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে বিষয়টি নিয়ে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।
পনেরো : সংসদীয় ব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক দল জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে দল থেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে সাধারণত সংসদীয় দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। আবার এটিও লক্ষণীয় যে, সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় বাংলাদেশে সব সময় বিজয়ী দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী করা হয় এবং তিনি সংসদনেতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এর ফলে এক ব্যক্তি তথা প্রধানমন্ত্রী একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। এ প্রবণতা রোধে সংবিধান সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে, একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দু’বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এ ছাড়াও সুপারিশ করা হয়, প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদনেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে বহুদলের ঐকমত্য থাকলেও বড়-ছোট দু-চারটি দল প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১৫ বছর করার পক্ষে মত দিয়েছে বলে জানা যায়। অপরদিকে, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তার রাজনৈতিক দলের প্রধান ও সংসদনেতা থাকা উচিত নয় বলে সংবিধান সংস্কার কমিশন যে সুপারিশ করেছে তা কিভাবে নিষ্পত্তি হয় তার জন্য আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।
ষোলো : বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদে সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যায়। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, একটি দল সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করে সহজে সংবিধান সংশোধন করে ফেলেছে। এমনকি সংবিধান সংশোধনের বিষয় নির্বাচনী ইশতেহারে কোনো উল্লেখ না থাকা সত্তে¡ও ব্যক্তির খেয়ালখুশি বা দলীয় স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। সংবিধানকে গণ্য করা হয় একটি দেশের নাগরিকদের সামষ্টিক অভিপ্রায়ের সর্বোচ্চ দলিল বা আইন। কিন্তু সংসদে ৪০ শতাংশ ভোট লাভ করে সংবিধান সংশোধন করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। বিভিন্ন দেশে সংবিধান চ‚ড়ান্ত অনুমোদন বা সংশোধনে গণভোটের বিধান রাখা আছে। বিশেষ করে সংবিধানের কতগুলো মৌলিক অনুচ্ছেদ সংশোধনে গণভোটের বিধান রাখা উচিত। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুমোদনে কোনো গণভোটের ব্যবস্থা ছিল না।
সংবিধান সংস্কার কমিশন একদিকে সুপারিশ করেছে, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ হলে সংবিধানের যেকোনো সংশোধনীর ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন প্রয়োজন হবে। কমিশন আরো সুপারিশ করেছে, প্রস্তাবিত সংশোধনী উভয় কক্ষে পাস হলে, এটি গণভোটে উপস্থাপন করা হবে। গণভোটের ফল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে, সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬, ও ১৪২ সংশোধনের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের অনুমোদনের পরে গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে। তবে উচ্চতর কক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে যদি ঐকমত্য না হয় সে ক্ষেত্রেও ওই সব অনুচ্ছেদ সংশোধনের বিষয়ে জাতীয় সংসদের অনুমোদনের পরে গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে।
সতেরো : সংবিধানের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী বর্তমানে রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দিতে পারেন। অতীতে ওই পদে নিয়োগে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক বিবেচনায় ক্ষমতাসীন দলের পছন্দের ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় সংবিধান সংস্কার কমিশন দুটো বিষয় বিবেচনায় রেখে সুপারিশ করেছে, আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ওই সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করেছে। অপরদিকে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন গঠন করতে কমিশন সুপারিশ করেছে। প্রধান বিচারপতি, আপিল বিভাগের পরবর্তী দু’জন জ্যেষ্ঠ বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের দু’জন জ্যেষ্ঠতম বিচারক, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সংসদ মনোনীত একজন নাগরিককে নিয়ে প্রস্তাবিত কমিশন গঠন করার জন্যও সুপারিশ করা হয়। ইতোমধ্যে এরূপ একটি কমিশন গঠিত হয়েছে বলে প্রকাশিত হয়েছে।
আঠারো : নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত প্রস্তাবে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘বাংলাদেশের সংবিধানে সীমিত সংখ্যক মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে মাত্র কয়েকটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কমিশন মনে করে, সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকারের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু সেগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয় এবং মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয় না। সংবিধান রাষ্ট্রকে এই নীতিগুলো অনুসরণ করে আইন প্রণয়নের নির্দেশ দিলেও ওই নির্দেশগুলো বাস্তবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, আদালত তা পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রাখেন না। নীতিগুলো এভাবে উপেক্ষা করায় সেগুলো কার্যত অর্থহীন অনুচ্ছেদে পরিণত হয়েছে, যা সংবিধানের সর্বোচ্চ মর্যাদার ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অন্যতম আদর্শ হলো- মানবাধিকারগুলো বিভাজনযোগ্য নয় এবং তাদের মধ্যে কোনো উঁচু-নিচু ভেদাভেদ করা যায় না। বিষয়টি সার্বিক বিবেচনায় নিয়ে কমিশন বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- বর্তমান সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকার এবং তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারগুলো সংশোধন করে ‘মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা’ নামে একটি একক অধিকারের সনদ গঠন করা, যা আদালতে বলবৎযোগ্য হবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার ও নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে বিদ্যমান তারতম্য দূর হয়। বিষয়টি এখনো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনায় আসেনি। আশা করা যায়, রাজনীতিকরা তাদের প্রজ্ঞা দিয়ে জাতির কল্যাণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
সংবিধান সংস্কারে সংশ্লিষ্ট কমিশন বিভিন্ন বিষয়ে আরো অনেক সুপারিশ করেছে। সেগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রথম দফার আলোচনা হয়েছে। সেখানেও বেশ কিছু বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। সুতরাং আমরা আশা করতে পারি, জাতির বৃহত্তর কল্যাণে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা তাদের দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে একটি জাতীয় সনদ প্রণয়নে সফল হবেন।
এরপর স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, জাতীয় সনদটি কিভাবে আইনি ভিত্তি দিয়ে সেটিকে সব রাজনৈতিক দলের জন্য বাধ্যতামূলক করা যাবে। কেউ বলেছেন, সংবিধান প্রণয়নে একটি গণপরিষদ গঠন করা যেতে পারে। আরো প্রস্তাব রয়েছে, জাতীয় সনদটি গণভোটে দিয়ে তার উপর নাগরিকদের অভিমত নেয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আলাদা গণভোটের আয়োজন না করে আগামী জাতীয় নির্বাচনের সাথে করা যেতে পারে। আরো একটি পরামর্শ রয়েছে, একটি আইনি কাঠামোর আওতায় আগামী সংসদকে একই সাথে গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদ হিসেবে গণ্য করে তাদের উপর সংবিধান সংশোধন বা পুনর্লিখন করা যেতে পারে।
লেখক : গবেষক ও সাবেক সচিব