সংবিধান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কেন
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশেষ করে সংবিধান সংস্কারে যে উপর্যুপরি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাতে রাজনৈতিক দলগুলো যে আন্তরিকতা ও সহনশীলতার সাথে বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিষ্পত্তির চেষ্টা করে যাচ্ছে তাতে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আগামীতে জনআকাক্সক্ষা বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে যাবে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি ড. আলী রীয়াজ বলেছেন, জুলাই মাসের মধ্যে জাতীয় সনদ বা জুলাই সনদ চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে [সূত্র : নয়া দিগন্ত, ১১ জুলাই ২০২৫]
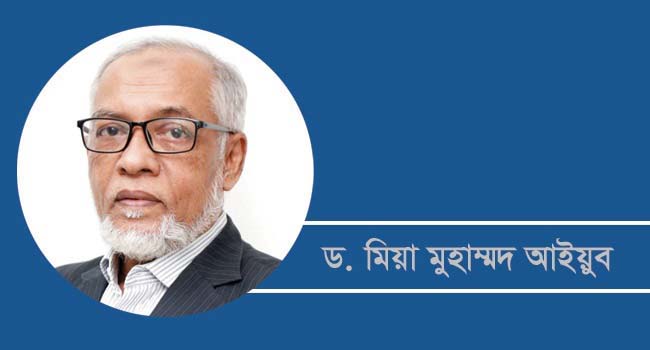
(দ্বিতীয় কিস্তি)
গত সপ্তাহে সংবিধান সংস্কার প্রসঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা, সংসদে নারী আসন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল সম্পর্কে মোট ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের হালনাগাদ তথ্যও দেয়া হয়েছিল। আমরা লক্ষ করছি, বেশ কয়েকটি সাংবিধানিক ইস্যুতে ইতোমধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে খবর প্রচারিত হয়েছে। আজকে সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।
সপ্তম : সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা। এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে-‘সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বিদ্যমান সংবিধানে সংসদ সদস্যদের বাধ্য করে যে, তারা যে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নে নির্বাচিত হয়েছেন, ওই দল প্রস্তাবিত যেকোনো নীতি বা সিদ্ধান্ত অকপটে মেনে নিতে। যদিও তাদের মতামত দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে, কিন্তু দলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। যদি তারা তা করেন তাহলে এর পরিণাম বেশ কঠোর, অর্থাৎ- সংসদে তাদের আসন স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্য হয়ে যাবে। সংবিধান দলের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের নামে সংসদ সদস্যদের স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে বাধা প্রদান করে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, যদিও দলত্যাগ (ফ্লোর ক্রসিং) আটকানো ছিল এ অনুচ্ছেদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, কিন্তু কার্যত এর প্রভাব এই উদ্দেশ্য ছাপিয়ে গিয়েছে। ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ফ্লোর ক্রসিংয়ের বিরুদ্ধে বিধানটি সংসদে গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী। স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্যে এ বিধান রাখা হলেও, এটি রাজনৈতিক আলোচনা ও দলীয় জবাবদিহিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলো একমত পোষণ করেছে যে, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদটি সংশোধিত হওয়া দরকার। দীর্ঘ আলোচনার পর সবাই একমত হয়েছে, জাতীয় সংসদে অর্থ বিল (বাজেট) ও সরকারের প্রতি আস্থাভোট ব্যতীত অন্যান্য সব ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা দলীয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবে। অবশ্য কোনো কোনো দল সংবিধান সংশোধন ও যুদ্ধ ঘোষণাসংক্রান্ত বিষয়কেও এর সাথে যোগ করার প্রস্তাব দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক একটি বিধানকে সংশোধনের বিষয়ে যে একমত পোষণ করেছে তা সংসদীয় রাজনীতিতে একটি গুণগত পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
অষ্টম : জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতির পদ বিরোধী দলকে দেয়ার ব্যাপারেও রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পর ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে যে, সংসদের গুরুত্বপূর্ণ চারটি স্থায়ী কমিটি যথা- পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, এস্টিমেশন কমিটি, পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটি ও প্রিভিলেজ কমিটির সভাপতির পদ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ও অন্যান্য কমিটির সভাপতি পদের ৫০ শতাংশ বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন দিতে বিধান করা হবে। সংসদে সরকারি দলের জবাবদিহির ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।
নবম : নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব এককভাবে নির্বাচন কমিশনের। কাজটি করা সহজ নয়। বিশেষ করে সবপক্ষকে খুশি করা বেশ কঠিন। নিকট অতীতে পতিত সরকার নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে এমন চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছিল যাতে প্রতিপক্ষকে হারানো সহজ হয়। বস্তুত, কাজটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান প্রয়োজন। এ জন্য নির্বাচন সংস্কার কমিশন জনসংখ্যাবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, ভূতত্ত্ববিদ ও জিআইএস বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে- কারিগরিভাবে কাজটি করতে জনসংখ্যা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা উচিত। তারা মনে করেন, আসন্ন নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের আওতায় এরূপ কমিটি গঠিত হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে প্রতি জনশুমারি বা ১০ বছর অন্তর নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটি কমিশন নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। এ কমিটি স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে বিতর্কের ঊর্র্ধ্বে থাকবে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে বলে জানা গেছে।
দশম : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন বিষয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি যেকোনো শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর আরোপিত দণ্ড মার্জনা, দণ্ড মওকুফ, দণ্ড হ্রাস, দণ্ড স্থগিত এবং দণ্ড বিলম্বের আদেশ দিতে পারেন। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে তা সর্বজনবিদিত। তখন রাজনৈতিক বিবেচনায় বিচার কাজ শেষ হওয়ার আগে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে, একই অপরাধীকে দু’বার ক্ষমা প্রদর্শনের ঘটনাও ঘটেছে। ক্ষমা প্রদর্শনের এ ঘটনাগুলো দেশে আইনের শাসনের ধারণাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এসব বিবেচনায় জাতীয় ঐকমত্যের সাথে আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলো একমত পোষণ করেছে যে, বিদ্যমান ব্যবস্থা সংশোধন করে আইনের আওতায় গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় দলগুলো একমত হয়েছে, ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন বিবেচনার আগে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও পরিবারের মতামত গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, ইসলামী আইনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার চাইলে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে বা নিঃশর্ত ক্ষমা করতে পারে। রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না। বিষয়টির ওপর ঐকমত্যের ফলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতির এরূপ ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বন্ধ হবে বলে আশা করা যায়।
একাদশ : বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গ। সংবিধান সংস্কার কমিশন ও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন উভয় সুপারিশ করেছে, উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ করে সব বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী আসন প্রবর্তন করা। সংবিধান সংস্কার কমিশনের মতে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতে থাকবে এবং দেশের সব বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হবে। হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ কোনোভাবে সুপ্রিম কোর্টের একক চরিত্রকে ক্ষুণ্ন্ন করবে না। স্মরণযোগ্য যে, ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা গ্রহণের পর ছয়টি হাইকোর্ট বেঞ্চ দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি রাষ্ট্রের ইউনিটারি পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক বিবেচনায় বেআইনি বলে রায় দিয়েছিলেন। কেউ কেউ ওই রায়ের উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু তারা ভুলে যান, কোনো আদালতের রায় চিরস্থায়ী নয়। শোনা যায়, ঢাকার নামকরা আইনজীবীদের প্রচেষ্টায় জেনারেল এরশাদের উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়েছিল। দেশের জনগণের কল্যাণে বিশেষ করে বিচারব্যবস্থা নাগরিকদের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশে বিদ্যমান ব্যবস্থার সংস্কার করে তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে। হাইকোর্টে প্রায় পাঁচ লাখ মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এমতাবস্থায় উচ্চ আদালত বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো মহল যুক্তি দিয়ে থাকে, ঢাকার বাইরে এতগুলো আদালত স্থাপিত হলে দক্ষ বিচারক ও আইনজীবীর অভাব দেখা দিতে পারে। এর বিপক্ষে যুক্তি হলো, দেশে এখন প্রচুর সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র পড়ানো হয় এবং অনেক আইন কলেজও রয়েছে। সাম্প্রতিককালে যুক্তরাজ্য থেকে অনেক তরুণ-তরুণী বার-এ্যাট-ল’ কোর্স করে দেশে ফিরেছেন। সুতরাং বিচারক ও আইনজীবীর সঙ্কট হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ ছাড়া বর্তমানে জেলা পর্যায়ে অনেক প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ আইনজীবীও রয়েছেন।
অপর দিকে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপনের সুপারিশ করেছে। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা বিবেচনায় ৬৫টির বেশি উপজেলায় এরূপ আদালত রয়েছে। আবার বিভিন্ন জেলার সদর উপজেলাগুলো জেলা সদরের সংলগ্ন হওয়ায় সেখানে উপজেলা আদালত স্থাপনের যৌক্তিকতা নেই। এসব বিবেচনায় রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে, বিদ্যমান ৬৫টি উপজেলার আদালত বহাল রেখে এবং সদর উপজেলাগুলো বাদ দিয়ে অন্যান্য উপজেলায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপন করা যেতে পারে।
দ্বাদশ : সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন- নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক পদে এবং কয়েকটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যেমন- দুর্নীতি দমন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগে সংবিধান সংস্কার কমিশন একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে একমত হয়নি। পরবর্তীতে ঐকমত্য কমিশন সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করে, ওই সব সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের পরিবর্তে একটি নিয়োগ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ওই কমিটি গঠিত হবে, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য বিরোধী দলের মনোনীত একজন সদস্য, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে। সংসদ ভেঙে গেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ কমিটির দায়িত্ব পালন করবে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো অনেকটা ঐকমত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কোনো কোনো দলের যুক্তি হচ্ছে- এর মাধ্যমে যেন প্রধানমন্ত্রী তথা নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস না পায়।
ত্রয়োদশ : দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা প্রসঙ্গ। বিদ্যমান সংবিধানের ১৪১ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ‘রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যেকোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১২০ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।’ তবে এরূপ ঘোষণার আগে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর প্রয়োজন হবে এবং তা পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। সংবিধানের ১৪১ (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকাকালে নাগরিকদের বেশ কিছু মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়ে থাকে।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রপতির ওপর এককভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দিতে রাজি নয়। এ ব্যাপারে সবাই একমত। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন প্রথমে প্রস্তাবিত জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের ওপর এ ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু ওই কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে জাতীয় সংসদে একটি সর্বদলীয় কমিটির সাথে আলোচনা করে অথবা মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরি অবস্থা জারি করা যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত ঐকমত্য এখনো হয়নি। তবে সবাই একমত হয়েছে যে, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবেন। সবার অভিমত হচ্ছে, ‘অভ্যন্তরীণ গোলযোগের’ কথাটি বাদ দিতে হবে, কারণ অতীতে এরূপ অজুহাতে রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য জরুরি অবস্থা জারি করা হতো।
রাজনৈতিক দলগুলো আরো একমত হয়েছে, জরুরি অবস্থাকে কোনোক্রমে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না এবং কতিপয় মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকলেও জনগণের জীবনের নিরাপত্তা ও কারো প্রতি নিপীড়ন-নির্যাতন না করার অধিকার স্থগিত করা যাবে না।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশেষ করে সংবিধান সংস্কারে যে উপর্যুপরি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাতে রাজনৈতিক দলগুলো যে আন্তরিকতা ও সহনশীলতার সাথে বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিষ্পত্তির চেষ্টা করে যাচ্ছে তাতে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আগামীতে জনআকাক্সক্ষা বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে যাবে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি ড. আলী রীয়াজ বলেছেন, জুলাই মাসের মধ্যে জাতীয় সনদ বা জুলাই সনদ চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে।
লেখক : গবেষক ও সাবেক সচিব