নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের অপরিহার্যতা
নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা হচ্ছে-সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অসদাচরণের জন্য পদচ্যুত করা যায়। কিন্তু অতীতে বেশ কয়েকটি প্রহসনের নির্বাচন হলেও নির্বাচন কমিশনকে কোনো প্রকার জবাবদিহি করতে হয়নি। দেশে এই প্রথমবারের মতো অন্তর্বর্তী নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সদস্যরা ও সচিবদের অপকর্মের জন্য আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়েছে। জনরোষের ঘটনাও দেখা গেছে যা কাক্সিক্ষত না হলেও বাস্তবতার উদাহরণ। এ ঘটনা থেকে নির্বাচনে সম্পৃক্ত সবার জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে।- ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব [আপডেট : নয়াদিগন্ত, ২৭ জুন ২০২৫]
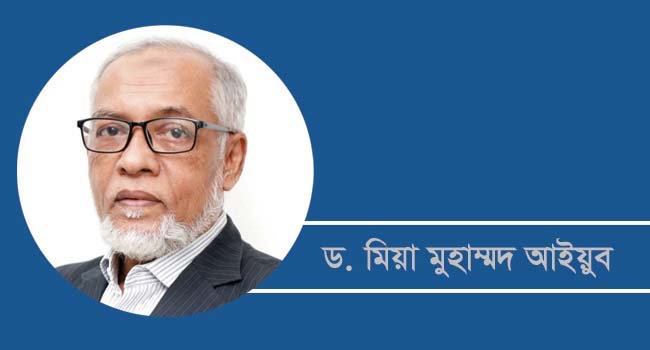
অতি সম্প্রতি দুই সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার যথাক্রমে- নুরুল হুদা এবং হাবিবুল আউয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিগত তিনটি জাতীয় নির্বাচন তথা ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের প্রহসনমূলক নির্বাচনের জন্য দায়ী নির্বাচন কমিশন চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবদের বিচারের আওতায় আনা হবে। উল্লেখ্য, এর আগে গঠিত নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন- উভয় এ বিষয়ে সুপারিশ করেছিল। সরকার সেই সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। তিন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে দু’জন গ্রেফতার হলেও এখনো কাজী রকিব উদ্দিন গ্রেফতার হননি। শোনা যায়, তিনি বয়োবৃদ্ধ ও পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে দিনাতিপাত করছেন।
সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদাকে গ্রেফতারের সময় তার প্রতি কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনতা তাকে অপমানিত করার জন্য যে আচরণ করেছে তা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। একজন ব্যক্তি অপরাধ করলে দেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী তাকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করতে হয়। এরপর বিধি মোতাবেক বিচারে তিনি যে শাস্তি প্রাপ্য হবেন তাকে তা দেয়া হবে। কিন্তু আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো সাধারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কাউকে অপমানিত করার অধিকার রাখে না। যে ঘটনাটি ঘটে গেছে সরকার ও সরকারের বাইরে সবাই তার নিন্দা করেছে। স্মরণযোগ্য যে, আদালতে দু’জন নিজেদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন এবং তা-ই স্বাভাবিক। তবে তাদের মুখ থেকে সত্যও উচ্চারিত হয়েছে। তারা বলেছেন, বিগত তিনটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে হয়নি এবং তাতে তাদের কিছু করার ছিল না। তাদের কিছু করার ছিল কি-না তা নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক করা যেতে পারে। হাবিবুল আউয়াল আদালতকে বলেছেন, এমনকি শেখ মুজিবও ১৯৭২ সালে ক্ষমতা গ্রহণের স্বল্প দিনের ব্যবধানে ১৯৭৩ সালে যে নির্বাচন দিয়েছিলেন তাও নিরপেক্ষ ছিল না। তিনি আরো বলেন, বিদ্যমান ব্যবস্থায় আগামী এক হাজার বছরেও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই।
আসলে কি তাই? দেশে ১৯৯১ সালের নির্বাচন সবচেয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মর্মে প্রায় সব মহলের স্বীকৃতি রয়েছে। এমনকি ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচন নিয়েও বড় ধরনের বিতর্ক নেই। ওই তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এর মাধ্যমে এটি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যে, বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অপরিহার্য। যখন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মডেল অন্যান্য দেশে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে, সে সময়ে ২০১০ সালে আওয়ামী লীগ আদালতের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। এরপর প্রহসনের তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
২০২৪ সালে জুলাই-আগস্টে ঘটে যাওয়া ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলে রাষ্ট্র সংস্কারের বিষয়টি সামনে আসে। পতিত সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এমনভাবে ধ্বংস করে গেছে, যার সংস্কার না করে একটি কার্যকর রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের বন্দোবস্ত করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করে। এর অন্যতম হচ্ছে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। ওই কমিশন যথাসময়ে সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করেছে। এরপর সরকার গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো নিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরির লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। ওই কমিশন বেশ কিছু দিন ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কমিশন অনেক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারলেও কতগুলো বিষয়ে এখনো মতপার্থক্য রয়ে গেছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজ আশা প্রকাশ করেছেন, আরো কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।
নির্বাচন সংস্কার কমিশন ১৮টি বিষয়ে সুপারিশ করেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- নির্বাচন কমিশন গঠনপ্রক্রিয়া, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনে স্বচ্ছতা, সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণে নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ গঠন, সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন, জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা, প্রবাসীদের ভোটদানের সুযোগ, নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহি, স্থানীয় সরকার নির্বাচন ইত্যাদি।
আমরা প্রথমে নির্বাচন কমিশন গঠনপ্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে পারি। বিদ্যমান ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশন গঠনে পৃথক আইন রয়েছে। সে অনুযায়ী, একটি সার্চ কমিটি (অনুসন্ধান কমিটি) গঠন করা হয় এবং তাদের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারকে নিয়োগ দেন। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মাত্র দুটো ক্ষেত্র ব্যতীত সব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য। সুতরাং সার্চ কমিটি ও নির্বাচন কমিশন গঠন করার ক্ষেত্রেও তিনি তার পরামর্শ নেবেন। দেখা যাচ্ছে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন সরকার সার্চ কমিটি ও নির্বাচন কমিশন গঠন করার ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশন ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগ দেয়ার জন্য একটি সাংবিধানিক পরিষদ (এনসিসি) গঠনের সুপারিশ করে। বিষয়টি নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পেরে একটি সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করে। সংশোধিত প্রস্তাবে এনসিসির পরিবর্তে ‘সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিয়োগ কমিটি’ গঠনের কথা বলা হয়েছে এবং তা গঠিত হবে প্রধানমন্ত্রী, দুই কক্ষের স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদের অন্যান্য বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, রাষ্ট্রপতির একজন প্রতিনিধি ও প্রধান বিচারপতির মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারকসহ সাত সদস্য নিয়ে। নতুন প্রস্তাবটি বিএনপিসহ কয়েকটি দল ব্যতীত অধিকাংশ দল সমর্থন করেছে। আগামী সপ্তাহের আলোচনায় নিরঙ্কুশভাবে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে কি-না তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হলে নির্বাচন কমিশন ও কয়েকটি সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রভাবমুক্ত নিয়োগ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্য রয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগপদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে যা নিরসনে সামনের আলোচনায় প্রচেষ্টা চালানো হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের অন্যতম একটি মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু অভিযোগ রয়েছেÑ বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে দলীয় সুবিধা বিবেচনায় বহু সংসদীয় এলাকার সীমানা পরিবর্তন করা হয়েছিল। বস্তুত সীমানা নির্ধারণের কাজটি বেশ জটিল এবং এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া দরকার হয়। আবার এর সাথে আদমশুমারির একটি সম্পর্ক রয়েছে। বহু দেশে প্রতি ১০ বছর অন্তর আদমশুমারি ও সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ করার বিধান রয়েছে এবং সে কাজটি একটি নিরপেক্ষ ও কারিগরিভাবে দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি কমিশন করে থাকে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ যেমন- ভুগোলবিদ, পরিসংখ্যানবিদ নিয়ে একটি কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে। প্রতি আদমশুমারির পরে সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা সম্পন্ন করার পর কমিশন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রস্তাবটি রাজনৈতিক দলগুলো সুবিবেচনা করতে পারে।
জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে ভোটার তালিকা তৈরি করা নির্বাচন কমিশনের আরেকটি মৌলিক দায়িত্ব। অতীতে ভোটার তালিকা সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়নি বলে নানাবিধ অভিযোগ ছিল। বস্তুত নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা থাকা অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় পরিচয়পত্রের একটি বিশাল তথ্যভাণ্ডার নির্বাচন কমিশনের হাতে রয়েছে। সুতরাং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজটি যদি নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে করতে পারে তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার বিষয়টি অনেকটা এগিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে একটি বিতর্ক রয়েছে যে, জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ কোন সংস্থার কাছে থাকবে। বর্তমানে তা নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পতিত সরকার সেটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করেছিল। একটি সুপারিশ রয়েছে যে, আলাদা একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করে জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।
ভোটার তালিকার সাথে আরেকটি বিষয় জড়িত রয়েছে; আর সেটি হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোটার করা এবং তাদের ভোট দেয়ার অধিকার ও সুযোগ দেয়া। সব মহল এ বিষয়ের সাথে একমত। তবে কাজটি মোটেই সহজ নয়। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশীদের ভোটার হওয়ার জন্য সুযোগ করে দেয়া একটি দুরূহ কাজ। যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই এবং জনগণকে কোনো সমাবেশ করার সুযোগ দেয় না সেসব দেশে বিষয়টি আরো কঠিন। তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজটি করা যেতে পারে। জানা যায় যে, নির্বাচন কমিশন প্রবাসীদের ভোটার করার কাজটি অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। এরপর প্রশ্ন আসবে তারা কিভাবে ভোট দেবেন। প্রচলিত পুরাতন পদ্ধতি হচ্ছে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দান এবং আরেকটি হচ্ছে অনলাইনে ভোট দেয়া। কোনো কোনো উন্নত দেশে অনলাইনে ভোট দেয়ার বিধান আছে। এর সাথে ত্রুটিমুক্ত প্রযুক্তিগত সুবিধা পাওয়ার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সে বিবেচনায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমবারের মতো পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দান চালু করা যেতে পারে।
আরেকটি বিষয় হচ্ছে- স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়। বর্তমানব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিষয় সরকার তথা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে। তবে ভোট গ্রহণের কাজটি সরকারের অনুরোধে নির্বাচন কমিশন করে থাকে। একটি বিষয়ে প্রায় সব দল একমত যে, স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব আইনগতভাবে সরকারের কাছ থেকে নির্বাচন কমিশনে ন্যস্ত করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নাকি পরে হওয়া উচিত- এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আবার নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে কতটা প্রস্তুত বা সক্ষম তাও বিবেচনার দাবি রাখে।
আরেকটি আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- জাতীয় সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হবে কি-না তা নিয়েও আলোচনা চলছে। এ ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের পক্ষে। আবার উভয় কক্ষের নির্বাচনপদ্ধতি কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কয়েকটি দল উভয় কক্ষে সমানুপাতিক হারে নির্বাচন চায়। সে ক্ষেত্রে যেসব সুবিধা-অসুবিধা যা রয়েছে তার আলোচনা চলছে। উচ্চতর কক্ষে সমানুপাতিক হারে নির্বাচন করার পক্ষে অধিকাংশই একমত।
রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন প্রদানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নির্বাচন কমিশনের কার্যপরিধিতে রয়েছে। তবে অতীতে বিভিন্ন কমিশন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেনি। সরকারি দল কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে কিংস পার্টি বা অখ্যাত ডামি পার্টিকে নিবন্ধন দিয়ে বিতর্কিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ মনে করেন, নিবন্ধনের শর্তাবলি শিথিল করা উচিত। আবার কারো কারো মতে, নিবন্ধন করার প্রক্রিয়াটি বাতিল করা উচিত; কারণ এসব শর্ত গণতান্ত্রিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।
নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা হচ্ছে- সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অসদাচরণের জন্য পদচ্যুত করা যায়। কিন্তু অতীতে বেশ কয়েকটি প্রহসনের নির্বাচন হলেও নির্বাচন কমিশনকে কোনো প্রকার জবাবদিহি করতে হয়নি। দেশে এই প্রথমবারের মতো অন্তর্বর্তী নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সদস্যরা ও সচিবদের অপকর্মের জন্য আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়েছে। জনরোষের ঘটনাও দেখা গেছে যা কাক্সিক্ষত না হলেও বাস্তবতার উদাহরণ। এ ঘটনা থেকে নির্বাচনে সম্পৃক্ত সবার জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে।
লেখক : গবেষক ও সাবেক সচিব