আশার জুলাই থেকে উদ্বেগের জুলাইয়ে
আলতাফ পারভেজ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ের গবেষক [প্রকাশ :প্রথম আলো, ১৬ জুলাই ২০২৫]
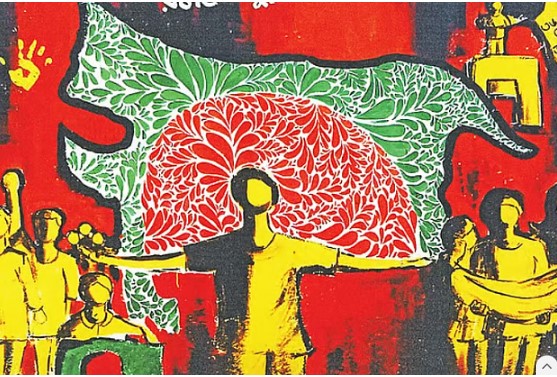
যে জুলাইয়ে প্রতিদিন শত শত তরুণ গণতন্ত্রের জন্য জীবন দিতেন, শত শত তরুণী নির্যাতনের ঝুঁকি নিয়ে গুন্ডারাজের বিরুদ্ধে রাজপথে নামতেন, এবারের জুলাই সে রকম কিছু নয় হয়তো। ২০২৪–এর গৌরবময় জুলাই স্বেচ্ছায় পবিত্র ইতিহাসে অন্তর্ধানে গেছে। দুই জুলাইকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা এখন ন্যায়সংগত কর্তব্যও বটে। যেভাবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধকে আলাদাভাবে বুঝতে পারা জরুরি ছিল।
২০২৪–এর জুলাই ‘দ্বিতীয় রিপাবলিকে’র স্বপ্ন নিয়ে হাঁটছিল। মনে হচ্ছিল, ১৯৭২–এ হারিয়ে ফেলা সাম্য-মৈত্রী-মানবিক মর্যাদার বিধ্বস্ত ইচ্ছাগুলো আমরা পুনর্গঠন করতে চলেছি। কিন্তু এখনকার জুলাইয়ে আমাদের সামনে অনেক বিপজ্জনক দৃশ্য হাজির।
নির্বাচন নিয়ে ধোঁয়াশা এবং পরবর্তী অবস্থা
খোদ প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্ধৃত করে তাঁর সহযোগীরা জুনে বলেছিলেন, ‘নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসেও হতে পারে।’ এ রকম প্রকাশ্য ঘোষণার পরও ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে বলে বিশ্বাস করা মানুষ এখনো খুব বেশি নয়। অথচ নির্বাচনের আশাকে খামছে ধরেই মানুষ অনিশ্চয়তায় ভরা সকাল-সন্ধ্যা পার করছেন। নির্বাচন হলো গণ–অভ্যুত্থান-উত্তর বাংলাদেশের ন্যূনতম চাওয়া। সেই ন্যূনতম চাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় সাম্য-মৈত্রী-মানবিক মর্যাদার বাকি প্রত্যাশাগুলো নিয়ে কেউ আর বাজি ধরতে চাইছে না।
নির্বাচনের টানাপোড়েনের কারণ নিয়ে বহুজনের বহুমত। কিন্তু তার ফলাফলে একমত হওয়া যায়। জনপ্রতিনিধিহীন জাতীয় ও স্থানীয় জীবনে বেনামি মামলা, রাহাজানি, জমিজমার বিবাদকে রাজনৈতিক রং দিয়ে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করার বিবিধ অনাচার প্রতিদিন গত জুলাইয়ের গৌরবকে লজ্জায় ফেলছে। পাথর দিয়ে মানুষ হত্যা থেকে খোদ মসজিদে ভিন্নমতের ইমামকে ছুরি মারার রোমহর্ষক অসহিষ্ণুতা দেখে ঘরে ঘরে মানুষ বিচলিত।
মাজার ভাঙাভাঙি আর নারীর হেনস্থার ভেতর দিয়ে এই গণসহিংসতা শুরু হয়েছিল। সেটাই এখন গণনৈরাজ্যের লক্ষণ নিয়ে শহর-গ্রামে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। সরকার সামাজিক নৈরাজ্য থামাতে সক্ষম কি না, সেই প্রশ্নের ইতিমধ্যে উত্তর মিলেছে। সেই কারণেই ভয় বাড়ছে, নির্বাচন রক্তপাতের পাশা খেলায় পরিণত হয়ে না যায়? এ রকমের সম্ভাব্য ফেব্রুয়ারি-এপ্রিলের মোকাবিলায় জাতীয় প্রস্তুতি কেমন? সশস্ত্র বাহিনী আর কত দিন মাঠে মাঠে থাকবে?
ট্রাম্পের অর্থনৈতিক যুদ্ধ মোকাবিলায় কী করবে বাংলাদেশ
বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের মূল আকর্ষণ এই মুহূর্তে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। সেখানকার উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষ কাজিয়ায় পিছিয়ে গেছে সংস্কারের জরুরি অনেক কিছু। এর মধ্যে অর্থনীতির তলপেট লক্ষ্য করে লাথি ছুড়লেন ট্রাম্প। তাঁর শুল্কবোমায় বাংলাদেশের প্রায় ৮০০ শিল্পপ্রতিষ্ঠান তীব্র বাণিজ্যসংকটের মুখে পড়েছে। তারকা ইমেজের ঊর্ধ্বতন অনেকে ওয়াশিংটন গেলেও শুল্ক ৩৭ থেকে ৩৫ ভাগের নিচে নামেনি। দর–কষাকষির পুরো প্রক্রিয়া কারা চালকের আসনে ছিলেন, আছেন এবং কী করেছেন, সে বিষয়ে ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তারা অনিশ্চয়তায় আছেন। বিবাদের সুরাহা না হলে ২৮ জুলাইয়ের পর যেসব পণ্যের চালান যুক্তরাষ্ট্রমুখী জাহাজে উঠবে, সেসবে নতুন শুল্কনীতির ছোবল পড়তে পারে।
দুর্যোগে নেতৃত্বের পরীক্ষা হয়। অর্থনৈতিক এই দুর্যোগ সামলানো এবং এর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক চাহিদা আছে কি না, সে বিষয়ে মানুষ জাতীয় নেতাদের কাছে পরিষ্কার কথাবার্তা শুনতে চায়। ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধ নিঃসন্দেহে আমাদের বিদেশনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জে অন্তর্ভুক্ত আছে চীন ও ভারতের সঙ্গে আমরা কীভাবে সম্পর্ক গড়তে চাই, সে-ই প্রশ্নও। নির্বাচনের আগে-পরে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের ভূরাজনৈতিক সক্ষমতার বড় চ্যালেঞ্জ হবে ওয়াশিংটন-নয়াদিল্লি-বেইজিংয়ের চাওয়া-পাওয়া সমন্বয় করতে পারা।
পুশইন ও নানা ধরনের বাণিজ্য-বাধা বাড়ানোর পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও হাসিমারায় সামরিক স্থাপনা শক্তিশালী করে ভারত বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের ওপর গরম নিশ্বাস ফেলে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কবোমাও একই রকম কিছু বলতে চায়। নির্বাচনের আগে-পরে এসব বিষয়ে বাংলাদেশ কী অবস্থান নেবে?
১২ মাসে নতুন করে প্রায় দেড় লাখ রোহিঙ্গাকে ঢুকতে দিয়ে ঢাকা তার কূটনীতির কী ব্যাখ্যা দিল, বোঝা মুশকিল। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্যে উগ্র রাজনীতির আলামতের কথা আসিয়ান দেশগুলোর সব রাজধানীতে ছড়িয়েছে ইতিমধ্যে। মেগনা বোল্ডিন নরম ভাষায় নানাজনকে যে সতর্ক করছেন, সেটা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার আছে।
বিচারপ্রক্রিয়া এগোচ্ছে, কিন্তু সামাজিক শান্তি-সমঝোতা?
নির্বাচন, রাজনৈতিক উগ্রবাদ ও শুল্কযুদ্ধের হালহকিকতের মতোই চলতি জুলাইয়ে ধোঁয়াশা চলছে আওয়ামী লীগের ভাগ্য নিয়ে। ১২ মের প্রজ্ঞাপন থেকে সবার জানা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দলটির নেতাদের বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের ‘যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ’ ঘোষণা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনও তাদের নিবন্ধন স্থগিত করেছে।
তবে ২১ জুন বিবিসিতে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎকার থেকে মনে হচ্ছে ‘আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে…লীগ নির্বাচনে থাকবে কি না, সেই সিদ্ধান্তের ভার নির্বাচন কমিশনের।’ নির্বাচন কমিশন এখনো এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। হয়তো ভবিষ্যতে জানাবে। তবে এ বিষয়ে একটা অস্পষ্টতা আছে এবং সমাজে বিতর্ক উঠেছে, লীগের সর্বোচ্চ নেতাদের বিচারাধীন অপরাধগুলোর দায় হিসেবে দলটির কর্মী-সমর্থকের নির্বাচনী পছন্দের অধিকারচর্চায় বাধা দেওয়া হবে কি না।
গত কয়েক মাসে যে জরিপগুলো হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, লীগের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সমর্থক রয়েছে এখনো সমাজে। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ডিসেম্বরের জরিপে দেখা গিয়েছিল, ৩৮ শতাংশ মানুষ এখনো ভোট কাকে দেবেন, সিদ্ধান্ত না নিলেও সিদ্ধান্ত নেওয়াদের মধ্যে ৯ শতাংশ লীগের সমর্থক। জুলাইয়ের শুরুতে গবেষণা সংস্থা সানেমের জরিপে লীগ–সমর্থক পাওয়া গেল ১৫ শতাংশ।
সমর্থক–সংখ্যা যা–ই হোক, প্রশ্ন উঠেছে, লীগের এই তৃণমূল-সমর্থকদের বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি কীভাবে জাতীয় রাজনীতিতে সমন্বিত করবে বা আদৌ এ বিষয়ে তারা কিছু ভাবছে কি না। লীগ–সমর্থকদের কাছেও একই রকম প্রশ্ন, তাঁরা ১৫ বছর প্রিয় দলের নেতৃত্বের কর্মকাণ্ডের দায় না নিয়ে, অনুশোচনা না করে আগামী দিনে কীভাবে জনসমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবেন?
এই দুই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও গুরুতর প্রশ্ন: বাংলাদেশে কি অনমনীয় প্রতিশোধমুখী রাজনীতিই চলতে থাকবে? আওয়ামী লীগ যেভাবে বিএনপি-জামায়াতকে দমনের নীতি নিয়ে ১৫ বছর চালিয়েছে, শেষোক্তরাও কি লীগ–সমর্থকদের প্রতি একই নীতি নিয়ে আগামী দিনগুলো চালাবে?
বিভেদবাদের পার্শ্বফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে জর্জরিত। রাজনীতিতে যুক্ত থাকা বেআইনি হলেও অন্তত মানসিকভাবে প্রায় সব জাতীয় প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বরতরা নীরবে হলেও জাতীয় রাজনীতির ধারায় বিভক্ত। নির্বাচনের পরও এটা অব্যাহত থাকবে।
ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সঙ্গে যুক্তদের বিশ্বাসযোগ্য বিচারের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে সামাজিক সমন্বয় বাড়ানোর কাজ এগোয়নি। আওয়ামী লীগের তরফ থেকে অনুশোচনা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। ফলে সব মিলিয়ে যেটা স্পষ্ট, গত দেড় যুগের অপরাধের বিচার হলেও ঐক্যবদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ভবিষ্যৎ অধরাই থাকবে। যারা নির্বাচনের পর ক্ষমতায় যাবে, তারা শান্তিতে দেশগঠনে মনঃসংযোগ করতে পারবে সামান্যই।
বৈষম্য না কমালে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে না
চব্বিশ ও পঁচিশের জুলাইয়ের মধ্যে বড় ব্যবধান গড়ার কথা ছিল বৈষম্য কমিয়ে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, এ বছর ‘হার্ডকোর পুওর’ বাড়বে ৩০ লাখ। এতে অতিদরিদ্র্য মানুষের হার ৯ শতাংশের ওপরে যাবে। সাধারণ দারিদ্র্যের পরিসংখ্যানও বেড়ে দাঁড়াল প্রায় ২৩ শতাংশে। এপ্রিলেই বিশ্বব্যাংক এসব জানাল। কোভিডের সময় ছাড়া বাংলাদেশে গত তিন দশকে দারিদ্র্য হার বাড়েনি।
গণ–অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী আমরা যখন উদ্যাপন করব, তখন সঙ্গে এ–ও মনে রাখা জরুরি, দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় চার কোটি এবং প্রায় এক কোটি তরুণ-তরুণী ছদ্মবেকার। অভ্যুত্থানের সরকার তাঁদের জন্য কী করল গত ১২ মাসে? বেকারদের কর্মসংস্থান বাড়াতে বিশেষ কিছু হলো কি? অথচ তরুণদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ‘লাল জুলাইয়ে’র গোড়াপত্তন।
সপ্তাহ দুয়েক আগে ৪৪তম বিসিএসে ১ হাজার ৬৯০ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। ৪৪ বিসিএসে আবেদন করেছিলেন ৩ লাখ ৫০ হাজার ৭১৬ জন। বাকি ৩ লাখ ৪৯ হাজার জন কী করবেন এখন? আগের বিসিএসেও ৪ লাখ ৩৩ হাজার জন চাকরি পাননি। এঁদের কথা কে ভাববে?
সরকারের অনেকের অর্থনীতিশাস্ত্রে দেশ-বিদেশে নামকরা ডিগ্রি থাকলেও মাঠের বাস্তবতা হলো, শিক্ষিত যুবাদের যেমন কাজের সুযোগ বাড়ছে না, নিচুতলার মানুষদেরও গত ১২ মাসে প্রকৃত মজুরি বাড়ার বদলে কমে গেছে। খালি পেটে থাকা মানুষের কাছে পার্লামেন্টে ‘কক্ষ’ একটা থাকবে না তিনটা থাকবে, সে বিষয় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এ রকম অনেক কিছুকে মহাগুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে শুনতে হচ্ছে প্রতিদিন।
লীগের শাসনামলেও ‘উন্নয়ন’–এর বিপুল গল্প শুনেছে মানুষ। শ্রোতাদের বোবা অসন্তোষের কথা অনেকেই টের পায়নি তখন। একই রকম বোবা ক্ষোভ আগামী দিনের সরকারকেও ভোগাতে বাধ্য। সম্ভাব্য সব দৃশ্য সেটা বলছে।
আলতাফ পারভেজ গবেষক ও লেখক